
ভয়ের বিস্তার থামায় কে
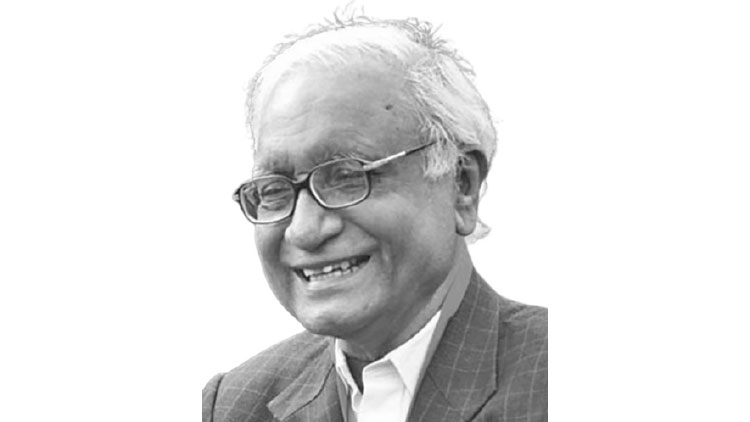 সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী:
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী:
ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার কাজে অতি নিকটের প্রতিবেশী ভারতও কিন্তু আমাদের সাহায্য করেনি। সাতচল্লিশের দেশভাগের সময়ে কংগ্রেস নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তারা তাদের রাষ্ট্রকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র দেবেন। পাকিস্তানের জিন্নাহ সাহেব শুরুতে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন বটে, কিন্তু সেখান থেকে পিছিয়ে আসতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন; কারণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিত্তিটাই ছিল ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু শাসকদল কংগ্রেসের শাসন ওই পথে এগোয়নি। ধর্মনিরপেক্ষতার একটি অভূতপূর্ব সংজ্ঞাই বরং তারা দাঁড় করিয়েছিলেন। সেটা হলো সব ধর্মের সমান মর্যাদা, যাকে আর যাই হোক কোনো দিক দিয়েই ধর্মনিরপেক্ষতা বলা যাবে না। জওয়াহেরলাল নেহরু ধর্মনিরপেক্ষতা চাইতেন, বল্লভভাই প্যাটেল ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার চরম বিরোধী এবং হিন্দু রাষ্ট্রের পক্ষে। প্যাটেলপন্থিদের শক্তি ছিল অধিক। তাদের ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছে; নেহরুপন্থিদের হটিয়ে দিয়ে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) রাষ্ট্রক্ষমতা পেয়ে গেছে। তাদের অঘোষিত অভিপ্রায় ‘বিদেশ থেকে আগত’ মুসলমানদের ফেরত পাঠানো। আর ঘোষিত রূপেই তো ওই পার্টির নেতা ও সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে দিয়েছেন যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী হয়ে এলে অমুসলিমদের তারা নিয়ে নেবেন। অর্থাৎ আমন্ত্রণই জানাচ্ছেন তাদের আসতে। এর বিপরীতে তিনি চাইছেন তথাকথিত ‘অবৈধ মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের’ ফেরত পাঠাতে। গত নির্বাচনের সময়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে তিনি তার নিজস্ব ভাষায় বলে দিয়েছিলেন যে ক্ষমতা পেলে বিজেপি সরকার বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের একজন একজন করে ধরবে এবং বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করবে।
পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য ভালো বিজেপি ক্ষমতা পায়নি। কিন্তু আসামে তো পেয়েছে। এবং সেখানে যারা একই সঙ্গে বাঙালি ও মুসলমান তারা নানা ধরনের নিগ্রহের শিকার হচ্ছে। বিজেপি ত্রিপুরাতেও জিতেছে এবং সেখানেও মুসলমান অধিবাসীরা অস্বস্তিতে পড়েছেন। ভারতের মুসলমানরা বিদেশ থেকে আসেননি; তারা স্থানীয়ই, কিন্তু যেহেতু তারা একে সংখ্যালঘু তদুপরি মুসলমান তাই অবজ্ঞার অবহেলার নীরব শিকার হয়েছে। দেখা গেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে তাদের আনুপাতিক হার অতি সামান্য; পুলিশ বিভাগে উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো নয়; কিন্তু জেলখানায় গেলে দেখা যাবে তারা রয়েছে ঠাসাঠাসি করে।
মোটকথা, ভারতের রাজনীতি-প্রবাহ বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য তো করছেই না, উল্টো বৈরিতাই করে চলেছে। ভারতের সঙ্গে পানিবণ্টন, অসম বাণিজ্য এবং সীমান্ত সংঘর্ষের অবসান ঘটেইনি, উল্টো বৃদ্ধিই পেয়েছে, তাতেও আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতা উৎসাহ পাচ্ছে।
তরুণদের দেশপ্রেমিক ও সৃষ্টিশীল করে তোলার জন্য যে সাংস্কৃতিক কাজ দরকার সেটা বাংলাদেশে এখন নেই। উন্নতির হুকুমদারিতে সংস্কৃতি দমিত হচ্ছে। আর তার কুফল সবচেয়ে গভীরভাবে বহন করছে তরুণ সমাজ।
নিরাপত্তার প্রশ্নটি অবশ্য আসে সবার আগে এবং সব নিরাপত্তার আগে আসে খাদ্যে নিরাপত্তার প্রশ্ন। করোনাকালে অধিকাংশ মানুষের আয়-উপার্জন কমেছে, কিন্তু দাম বেড়েছে খাদ্যের। মানুষ রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন। অনেকের জন্যই দশাটা খাবি খাওয়ার।
পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নিরাপত্তার সব উদ্যোগটাই দাঁড়ায় ব্যক্তিগত এবং মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁকটা থাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংগ্রহের দিকে। খবরটা অনেকেই পড়ে থাকবেন যে কেন্দ্রীয় পাট গবেষণা কেন্দ্রের একজন অবসরপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আনোয়ার শহিদ তার নাম, নিরাপত্তার জন্য সম্পত্তি সংগ্রহের ‘অপরাধে’ খুন হয়েছেন। একসময়ে তিনি কাজ করতেন দিনাজপুরে; ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে তিনি জমিজমা কিছু কিনেছিলেন, ভবিষ্যতের কথা ভেবে। যার মাধ্যমে কিনেছিলেন আপনজন হিসেবে তাকেই দিয়েছিলেন দেখাশোনা করতে। ওই আপনজন জমি থেকে আয়ের একটা অংশ মালিক ভদ্রলোককে নিয়মিত পৌঁছে দেবে এটাই ছিল শর্ত। আপনজনটি ছোটখাটো ব্যবসা করত, তার জন্য শহিদ সাহেবের কাছ থেকে কর্জ হিসেবে কয়েক লাখ টাকা নেয়। আপনজনটি এর মধ্যে মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে। তাই টাকা দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। টাকার জন্য আনোয়ার শহিদ তাগাদা দিচ্ছেন। শহিদ সাহেব বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু বিয়ে সফল হয়নি, তার কোনো সন্তানও নেই। আপনজনটি দেখল যে শহিদ সাহেবের তাগাদা থেকে অব্যাহতি পাওয়া তো বটেই তার সম্পত্তির মালিক হওয়াও সম্ভব যদি তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্যে সে ভাড়াটে খুনি জোগাড় করে। খুনিকে নিয়ে ঢাকায় আসে। সরল বিশ্বাসী শহিদ সাহেবকে ফোন করে ডেকে আনে, টাকা দেবে বলে। তিনি এলে শ্যামলী এলাকার এক গলিতে তার সঙ্গে আলাপের ভান করে, আর সেই ফাঁকে খুনিটি শহিদ সাহেবের বুকে ছুরি চালিয়ে তাকে হত্যা করে এবং দুজনে মিলে পালিয়ে যায়। পরে অবশ্য তারা ধরা পড়েছে। তবে তাতে আনোয়ার শহিদের কি-ইবা আসে যায়?
রাষ্ট্র নিরাপত্তা দেবে বলে; নিরাপত্তার জন্য নানা ধরনের আইন আছে, বাহিনী রয়েছে, আছে আদালত। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। বাংলাদেশ এরই মধ্যে ডিজিটাল যুগে পৌঁছে গেছে; কিন্তু এই প্রযুক্তির অপব্যবহার যাতে না ঘটে, ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র কারও স্বার্থেরই যাতে হানি না হয়, আইনের ঘোষিত উদ্দেশ্য সেটাই। অপরাধীদের বিচারের জন্য যে সাইবার ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে তাতে রুজু করা মামলাগুলোর শতকরা ৯৭টিই নাকি খারিজ হয়ে গেছে। রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। সেটা পরের ব্যাপার; কিন্তু অভিযুক্তকে তো তদন্তের আগেই কারাগারে চলে যেতে হয়, থাকতে হয় রিমান্ডে। অভিযুক্ত ও আইনজীবীদের কারও কারও অভিজ্ঞতা এই রকমের যে, বাদীর সঙ্গে রাজনৈতিক, সামাজিক বা আর্থিক আপস-মীমাংসায় পৌঁছাতে হয়। আর বিচারের প্রক্রিয়ায় যে আর্থিক শারীরিক ও সামাজিক দুর্গতি ঘটে তার তো কোনো ক্ষতিপূরণই নেই। মিথ্যা মামলা করা দ-নীয় অপরাধ বটে, কিন্তু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মিথ্যা মামলাকারীদের শাস্তির কোনো সুনির্দিষ্ট ধারা নেই। ওদিকে আবার সংক্ষুব্ধ নয় কিংবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়নি এমন ব্যক্তিও মানহানির মামলা ঠুকে দিতে পারে। আইনটি সংস্কারের দাবি উঠেছে, কিন্তু শোয়ার লোক নেই।
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি আইনও কার্যকর অবস্থায় আছে। এ আইনে মামলা হলে পুলিশ তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করতে পারে। যেমনটা ঘটেছিল ফটোগ্রাফার শহিদুল আলমের বেলায়। শহিদুল আলম একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এবং আন্তর্জাতিক মানের ফটোগ্রাফার। আমাদের স্মরণে আছে ২০১৮ সালে সড়কে দুজন শিক্ষার্থী বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যায়; এতে ব্যাপক ছাত্রবিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ঢাকা শহরের ধানম-ি এলাকায় ছাত্রদের বিক্ষোভে পুলিশের সামনেই হেলমেটে সুজ্জিত গু-াবাহিনী দমন-পীড়ন চালায়। শহিদুল আলম সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ছবি তুলছিলেন; আল জাজিরা টেলিভিশনের লোকরাও ছিল; তাদের অনুরোধে শহিদুল আলম তাদের একটি সাক্ষাৎকার দেন।
গণমাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর অপপ্রচার করেছেন এই অভিযোগে পুলিশ তার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেয়। গভীর রাতে বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে দৈহিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। এবং পরে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এতে দেশে তো বটেই বিশ্বের নানা স্থানে প্রতিবাদ ওঠে; প্রতিবাদকারীদের ভেতর বারোজন নোবেল পুরস্কারবিজয়ীও ছিলেন। সাড়ে তিন মাস জেলে কাটানোর পরে তিনি জামিনে মুক্ত হন। শহিদুল আলম জামিন পেয়েছেন জনমতের চাপে। জামিন পাওয়ার চেয়েও অনেক বড় ঘটনা তার ওপর দৈহিক নির্যাতন এবং তাকে আটকে রাখা। ওই স্তরের একজন মানুষ যদি ‘সাইবার অপরাধে’ অতসহজে হেনস্তা হন, তাহলে অন্যদের হালটা কী? আর এই বার্তা তো রটে যাবেই, গেছেও, যে গণমাধ্যমে এমন বক্তব্য দেওয়া একেবারেই অনুচিত যা সরকারের পছন্দ নয়।
ভয়ের বিস্তার থামায় কে? সরকারের দিক থেকে ভয়কে উৎসাহিত করা তো খুবই সুবিধাজনক।
লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
উপদেষ্টা সম্পাদক : আবু তাহের
প্রকাশক ও প্রধান সম্পাদক : আবদুল আজিজ
সম্পাদক: বিশ্বজিত সেন
অফিস: কক্সবাজার প্রেসক্লাব ভবন (৩য় তলা), শহীদ সরণি (সার্কিট হাউজ রোড), কক্সবাজার।
ফোন: ০১৮১৮-৭৬৬৮৫৫, ০১৫৫৮-৫৭৮৫২৩ ইমেইল : news.coxsbazarvoice@gmail.com
Copyright © 2025 Coxsbazar Voice. All rights reserved.