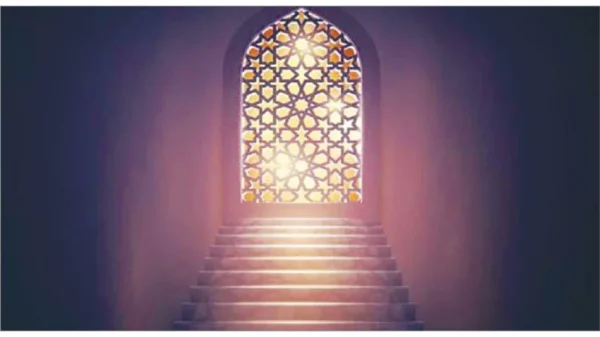মঙ্গলবার, ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:৪৮ অপরাহ্ন
দেশ এখন বাহাদুরি ও চাটুকারিতার

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী:
বঙ্গভূমি এখন বাহাদুরির ও চাটুকারিতার। এখানে হাতি, পাখি, নদী, বন, কোনো কিছুই নিরাপদে নেই, সবচেয়ে কম নিরাপদে আছে মানুষ। বাংলাদেশের বাহাদুরি এখন মানুষকে রক্ষা করাতে নয়, অবমাননা ও হত্যা করাতে। চাটুকারিতা এ দেশে নতুন কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু এখন প্রকাশ্যে, গণমাধ্যমের সাহায্যে, যে ধরনের চাটুকারিতা চলছে তেমনটা আগে কখনো দেখা যায়নি। খ্যাতিবান, বিদ্বান, বুদ্ধিমান লোকেরা এ কাজ করেন লজ্জাবিহীনভাবে। চাটুকারিতা পরিণত হয়েছে বাহাদুরিতে। চাটুকারিতা চলে সরকারের এবং চলে সরকার যে-ব্যবস্থার কারণে টিকে থাকে সেই ব্যবস্থার। মোটরসাইকেল তাকে একটা কিনে দেওয়া হয়েছিল, আরও দামি একটা চাই, না পাওয়াতে কিশোর পুত্রটি তার বাবা ও মায়ের গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দগ্ধ বাবা মারা গেছেন, মা যন্ত্রণায় কাঁদছেন। এ রকম খবর কোনো প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করে বলে মনে হয় না। ধরে নেওয়া হয় এটা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। কেননা প্রতিনিয়ত এ রকমের ঘটনা ঘটছে, পরেরটির ভয়াবহতা ছাড়িয়ে যাচ্ছে আগেরটিকে। বাবা মারছে মাকে, মা মেরে ফেলছে ছেলেকে। সহিংসতা এখন ঘরে ঘরে। প্রতিক্রিয়া জানাবার ফুরসৎ নাই।
কেবল যে হত্যা তা তো নয়, আত্মহত্যার সংখ্যাও বাড়ছে। আত্মহত্যাকারীদের কাপুরুষ বলার রেওয়াজ আছে। তারা পরাজিত, জীবনের ভার বহন করতে অক্ষম, তাই নিজেই নিজেকে হত্যা করছে, এ ব্যাখ্যা মোটেই অযথার্থ নয়। কিন্তু আত্মহত্যা করতে সাহসও লাগে, কাজটা সহজ নয়, এবং মানুষের জীবন দুটি নয়, একটিই। বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা শুরু হয়েছিল, এই তৎপরতার সবচেয়ে বিপজ্জনক দিকটা হলো এই যে, জঙ্গিরা আত্মহত্যায় ভয় পায় না। ওইখানে তারা খুবই সাহসী। আর যে লোক মরতে সাহস করে তাকে বাঁচায় কে, তার হাত থেকে বাঁচেই বা কে?
তবে এটা ঠিক যে, আত্মহত্যার মূল কারণ হলো হতাশা। দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা যে বাড়ছে তার কারণ হতাশা বাড়ছে। হতাশ যারা তারা সবাই আত্মহত্যা করে না, অধিকাংশই জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দুলতে থাকে, ঝিমায়, বোঝা হয়ে পড়ে নিজের কাছে, এবং সংসারের কাছে। দুঃসহ যন্ত্রণায় যারা স্থির থাকতে পারে না তারাই দুঃসাহসী পদক্ষেপটা নিয়ে ফেলে, শেষ করে দেয় নিজেকেই। এ রকম লোকের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে। তুলনায় মেয়েরাই ওই পথে বেশি সংখ্যায় যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক যে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল এবং চিরকুটে লিখে রেখে গেছিল যে, তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়, সে তো অভিযুক্ত করে রেখে গেল তার সব উত্ত্যক্তকারীদের, যাদের মধ্যে অতি আপন বলে যার ওপর সে ভরসা করেছিল সেও আছে। লোকটিকে সে বিয়ে করেছিল ভালোবেসে। মেয়েটি তো আকাশের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল না। আত্মহত্যা করছে এখন বাংলাদেশের কৃষকও। জীবনের বোঝা তাদের অনেকের কাছেই এখন ভয়াবহ এক যন্ত্রণা। পরিসংখ্যান সব খবর সঠিকভাবে দেয় না, তবু যা দিচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে আগে যেখানে বছরে গড়পড়তা দশ হাজার মানুষ নিজের প্রাণ নিজের হাতে শেষ করে দিয়েছে, সেখানে গত বছরে তাদের সংখ্যা ছিল পনেরো হাজার। আগামী বছরে এ সংখ্যা বাড়বে না, এমন মনে করার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই।
মার খাচ্ছে প্রকৃতিও। পৃথিবীজুড়ে পুঁজিবাদী কুঠার প্রকৃতিকে নিত্যদিন রক্তাক্ত করছে। মুনাফার লোভে, মুনাফার খোঁজে। প্রকৃতিরও প্রাণ আছে, সে মরে যেতে প্রস্তুত নয়, ঘা দিলে সেও ফিরতি ঘা দিতে চায়, দিচ্ছেও। ধরণী তপ্ত হয়েছে, সমুদ্রের পানির স্তর ওপরে উঠছে। খরা, প্লাবন, টাইফুন সবই দেখা দিয়েছে মারাত্মক আকারে। বিপন্ন প্রকৃতি সবাইকেই আঘাত করতে চায়, কিন্তু তার সেই আঘাতে গরিব মানুষই মারা পড়ে সবার আগে। মারা পড়ে গরিব দেশও। বাংলাদেশে প্রকৃতি প্রতিশোধ গ্রহণের অভিনব কিছু প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। বৃক্ষমানব ও বৃক্ষশিশুর খবর পাওয়া গেছে। বৃক্ষ উৎপাটিত হচ্ছে, উৎপাটিত হয়ে সে বুঝি ঢুকে পড়ছে এমন কি মানুষের দেহের ভেতরও। প্রতিশোধ, নাকি আশ্রয়ানুসন্ধান? ওদিকে জন্মবৃদ্ধ মানুষেরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। আমরা সাধারণত অতিদ্রুতই বৃদ্ধ হই, এবং বৃদ্ধ অবস্থায় শিশুর মতো আচরণ করি। এটা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু শিশু জন্মাচ্ছে বার্ধক্যের লক্ষণ নিয়ে অথবা চার বছর বয়সের শিশু ষাট বছরের বৃদ্ধের অবয়ব পেয়ে যাচ্ছে এটা নতুন ঘটনা। এ কী সমগ্র দেশের ভেতরের ক্লান্তির প্রতীকী প্রকাশ? বাংলাদেশে তারুণ্য ভীষণভাবে বিপদগ্রস্ত এবং বার্ধক্য মানসিকভাবে সন্তুষ্ট থাকছে না, শারীরিক রূপ পরিগ্রহ করছে, জন্মবৃদ্ধের আগমন হয়তো এই বাস্তবতারই প্রতীক। বায়ুদূষণের কারণে এক বছরে মারা গেছে সাঁইত্রিশ হাজার মানুষ। বজ্রপাত আমাদের জন্য নতুন কোনো ঘটনা নয়; বজ্রপাতকে অভিশাপ হিসেবেই দেখা হতো। তোমার মাথায় ঠাটা পড়–ক, এমন কামনা শত্রুর জন্য করাটা নিয়ম ছিল আমাদের সমাজে; এখন প্রকৃতিই ঠাটা ফেলছে, শোধ নিচ্ছে মানুষের ওপর। এই গরিব দেশে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। একদিনেই সাতাশজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল, সেদিন সড়ক দুর্ঘটনাতেও অতজন প্রাণ হারায়নি। মারা গেছে যারা তারা সবাই গরিব মানুষ, আশ্রয়হীন, অথবা বিপজ্জনক স্থানে বসবাসকারী। প্রকৃতি শোধ নিচ্ছে, তবে প্রকৃতিও দেখা যাচ্ছে ধনীদের সমীহ করে, অথবা বাধ্য হয় সমীহ করতে। প্রকৃতিও ধনীদের মতোই, গরিবের ওপরই চোটপাট করে বেশি বেশি করে। গরিব দেশের গরিবদের মারে সে অতিসহজে। গরিবের বিপদ চতুর্দিকে।
উন্নতি তো হচ্ছে। অবশ্যই। কিন্তু সে উন্নতির চরিত্রটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সেটা প্রাইভেট গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধির মতোই, পাবলিকের রেলওয়েকে যে কোণঠাসা করতে ভালোবাসে। এই উন্নতি হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ের, চারদিকে যার দুঃসহ ট্র্যাফিক জ্যাম; পথ অবরুদ্ধ, যেমন প্রবেশের তেমনি নির্গমনের। ঢাকার মেয়রদের একজন ঘোষণা দিয়েছিলেন ফুটপাত থেকে হকাররা উঠে না গেলে উন্নয়নের স্বার্থে তাদের ওপর দিয়ে তিনি বুলডোজার চালিয়ে দেবেন। এখানকার সব উন্নতিই ওই বুলডোজার-মার্কা। পুঁজিপাট্টা হারিয়ে সন্ত্রস্ত হকাররা কাঁদতে কাঁদতে উঠে যাবে বুঝলাম, কিন্তু যাবেটা কোথায়? খাবে কী? সে চিন্তা অন্য কারও নয়, হকারদের নিজেদের ছাড়া।
উন্নতির অন্তর্নিহিত দর্শনটা পুঁজিবাদী, এই দর্শনের বাস্তবায়নে যত উন্নতি হবে তত বাড়বে বৈষম্য। হকার উচ্ছেদ হবে, দেখা দেবে শপিংমল, যেখানে গরিব মানুষ কেনাকাটা দূরের কথা, ঢুকতেই সাহস পাবে না। বলা হচ্ছে ভিক্ষুক উচ্ছেদ করা চাই, কিন্তু মানুষ কেন ভিক্ষুক হয় সেটা ভাবা হচ্ছে না। ধনীর উন্নতি যে গরিবের ভিক্ষাবৃত্তির কারণ সেটা তো মিথ্যা নয়। তাহলে? তা ছাড়া আমাদের ধনীরাও তো মনে মনে বড় বড় ভিক্ষুক, তারা বিদেশের মুখাপেক্ষী, ক্ষণে ক্ষণে বিদেশে যায়, পারলে স্থায়ী বসতি গড়ে। রাষ্ট্রের মালিকরা হাত পেতে বসে থাকেন বিদেশি সাহায্যের আশায়। শাসক শ্রেণিকে ভরসা করতে হয় বিদেশিদের সমর্থনের ওপর, বিনিময়ে তারা দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেন প্রতিযোগিতামূলকভাবে।
শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতির দৃশ্যমান ছবি পাওয়া যাবে। শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু গুণ? শিক্ষামন্ত্রী জিপিএ ৫-এর বৃদ্ধি নিয়ে প্রতিবছর সন্তোষ প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু সম্প্রতি দেখা গেল তিনিও সংশয়ে পড়েছেন, বলছেন শুধু পরিমাণে কুলাবে না গুণগত মানও বৃদ্ধি করা চাই। মান কিন্তু বাড়েনি, ধারণা করা হয় যে সেটা নিম্নগামী। ধারণা নয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। এইচএসসিতে সেরা ফল করেছে যারা তারাই কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার মতো বুকের পাটা রাখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও সামাজিকবিজ্ঞান শাখায় এ বছর ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিয়েছিল ৩৩ হাজার, পাস করেছে ৩ হাজার, ৩০ হাজারই ফেল। শিক্ষামন্ত্রীর সেটা অজানা থাকার কথা নয়।
না, মানবৃদ্ধির কোনো কারণ নেই। শিক্ষার কেন্দ্রে থাকেন শিক্ষক। উপযুক্ত শিক্ষক যে আমরা পাচ্ছি না সেটা বলাই বাহুল্য। শিক্ষকের নিয়োগের ক্ষেত্রে ঘুষ ও দলীয় পক্ষপাতিত্বের প্রমাণিত অভিযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগের নতুন এক পদ্ধতি চালু করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। পদ-প্রার্থীদের নাকি লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে ও সংগ্রহ করতে হবে পুলিশের সার্টিফিকেট। যার সরল অর্থ দাঁড়াবে মেধাবীদের শিক্ষক হতে নিরুৎসাহিতকরণ। মেধাবান ও পরীক্ষিতদের জন্য পুনরায় লিখিত পরীক্ষা অমর্যাদার ব্যাপার। আর পুলিশের রিপোর্ট তো ভীষণরকমের বিপজ্জনক। লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা কোনোকালেই ছিল না। গোয়েন্দা রিপোর্ট পাকিস্তান আমলে চালু ছিল, এবং ওই ধরনের কার্যক্রম চালু থাকাটা ছিল অন্যতম কারণ, যে জন্য ওই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমাদের বিক্ষোভ গড়ে উঠেছিল এবং রাষ্ট্রটি ভেঙে আমরা বের হয়ে এসেছি। এখন চেষ্টা চলছে পুরনো ব্যবস্থাকে ফেরত আনার। এই পুলিশি কার্যক্রম দুর্নীতি ও উৎপীড়ন উভয়কেই প্রসারিত করে দেবে। আমরা আশা করব সিদ্ধান্তটি বাতিল করা হবে, কিন্তু ভরসা করি না, কারণ প্রতিবাদকারীদের সংখ্যা ক্রমে কমছে, তদবিপরীতে সংখ্যা বাড়ছে চাটুকারদের।
বিশ্ববিদ্যালয় তো পরে আসবে, শিক্ষার ভিত্তিটাই তো দুর্বল। প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না, মাধ্যমিক শিক্ষা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত। শিক্ষকদের মান এবং ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত উন্নত না হলে শিক্ষার মান বাড়বে এ রকম ভাবার কোনো কারণই নেই। নিয়োগ সুষ্ঠু নয়, নিয়োগের পরে প্রশিক্ষণ নেই। জবাবদিহিতা উঠে গেছে। প্রতিবেদন বলছে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার ভেতর বাংলাদেশের অবস্থান সবচেয়ে খারাপ। বাজেটে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ কোনো মতেই বাড়ানো যাচ্ছে না।
লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ভয়েস/আআ